 জীবনানন্দ দাশ। জন্ম: ১৮ই ফেব্রুয়ারি ১৮৯৯ বরিশাল – মৃত্যু: ২২শে অক্টোবর ১৯৫৪ বঙ্গাব্দ: ৬ই ফাল্গুন ১৩০৫ – ৫ই কার্তিক ১৩৬১। বিংশ শতাব্দীর অন্যতম প্রধান আধুনিক বাংলা কবি। তিনি বাংলা কাব্যে আধুনিকতার পথিকৃৎদের মধ্যে অগ্রগণ্য। মৃত্যুর পর থেকে শুরু করে বিংশ শতাব্দীর শেষ ধাপে তিনি জনপ্রিয়তা পেতে শুরু করেন এবং ১৯৯৯ খ্রিস্টাব্দে যখন তাঁর জন্মশতবার্ষিকী পালিত হচ্ছিল ততদিনে তিনি বাংলা সাহিত্যের জনপ্রিয়তম কবিতে পরিণত হয়েছেন। তিনি প্রধানত কবি হলেও বেশ কিছু প্রবন্ধ-নিবন্ধ রচনা ও প্রকাশ করেছেন। তবে ১৯৫৪ খ্রিস্টাব্দে অকাল মৃত্যুর আগে তিনি নিভৃতে ১৪টি উপন্যাস এবং ১০৮টি ছোটগল্প রচনা গ্রন্থ করেছেন যার একটিও তিনি জীবদ্দশায় প্রকাশ করেননি। তাঁর জীবন কেটেছে চরম দারিদ্যের মধ্যে। বিংশ শতাব্দীর শেষার্ধ কাল অনপনেয়ভাবে বাংলা কবিতায় তাঁর প্রভাব মুদ্রিত হয়েছে। রবীন্দ্র – পরবর্তী কালে বাংলা ভাষার প্রধান কবি হিসাবে তিনি সর্ব সাধারণ্যে স্বীকৃত।
জীবনানন্দ দাশ। জন্ম: ১৮ই ফেব্রুয়ারি ১৮৯৯ বরিশাল – মৃত্যু: ২২শে অক্টোবর ১৯৫৪ বঙ্গাব্দ: ৬ই ফাল্গুন ১৩০৫ – ৫ই কার্তিক ১৩৬১। বিংশ শতাব্দীর অন্যতম প্রধান আধুনিক বাংলা কবি। তিনি বাংলা কাব্যে আধুনিকতার পথিকৃৎদের মধ্যে অগ্রগণ্য। মৃত্যুর পর থেকে শুরু করে বিংশ শতাব্দীর শেষ ধাপে তিনি জনপ্রিয়তা পেতে শুরু করেন এবং ১৯৯৯ খ্রিস্টাব্দে যখন তাঁর জন্মশতবার্ষিকী পালিত হচ্ছিল ততদিনে তিনি বাংলা সাহিত্যের জনপ্রিয়তম কবিতে পরিণত হয়েছেন। তিনি প্রধানত কবি হলেও বেশ কিছু প্রবন্ধ-নিবন্ধ রচনা ও প্রকাশ করেছেন। তবে ১৯৫৪ খ্রিস্টাব্দে অকাল মৃত্যুর আগে তিনি নিভৃতে ১৪টি উপন্যাস এবং ১০৮টি ছোটগল্প রচনা গ্রন্থ করেছেন যার একটিও তিনি জীবদ্দশায় প্রকাশ করেননি। তাঁর জীবন কেটেছে চরম দারিদ্যের মধ্যে। বিংশ শতাব্দীর শেষার্ধ কাল অনপনেয়ভাবে বাংলা কবিতায় তাঁর প্রভাব মুদ্রিত হয়েছে। রবীন্দ্র – পরবর্তী কালে বাংলা ভাষার প্রধান কবি হিসাবে তিনি সর্ব সাধারণ্যে স্বীকৃত।
 জীবনানন্দ দাশ ১৮৯৯ খ্রিস্টাব্দে বাংলাদেশের দক্ষিণ প্রান্তের জেলাশহর বরিশালে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পূর্বপুরুষেরা ছিলেন ঢাকা জেলার বিক্রমপুর পরগণা নিবাসী। তাঁর পিতামহ সর্বানন্দ দাশগুপ্ত (১৯৩৮-৮৫) বিক্রমপুর থেকে স্থানান্তর ক্রমে বরিশালে নিবাস গাড়েন। সর্বানন্দ দাশগুপ্ত জন্মসূত্রে হিন্দু ছিলেন; পরে ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষা নেন। তিনি বরিশালে ব্রাহ্ম সমাজ আন্দোলনের প্রাথমিক পর্যায়ে অংশগ্রহণ করেন এবং তাঁর মানবহিতৈষী কাজের জন্যে সমাদৃত ছিলেন। জীবনানন্দের পিতা সত্যানন্দ দাশগুপ্ত সর্বানন্দের দ্বিতীয় পুত্র। সত্যানন্দ দাশগুপ্ত (১৮৬৩-১৯৪২) ছিলেন বরিশাল ব্রজমোহন স্কুলের শিক্ষক, প্রাবন্ধিক, বরিশাল ব্রাহ্ম সমাজের সম্পাদক এবং ব্রাহ্মসমাজের মুখপত্র ব্রাহ্মবাদী পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদক।
জীবনানন্দ দাশ ১৮৯৯ খ্রিস্টাব্দে বাংলাদেশের দক্ষিণ প্রান্তের জেলাশহর বরিশালে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পূর্বপুরুষেরা ছিলেন ঢাকা জেলার বিক্রমপুর পরগণা নিবাসী। তাঁর পিতামহ সর্বানন্দ দাশগুপ্ত (১৯৩৮-৮৫) বিক্রমপুর থেকে স্থানান্তর ক্রমে বরিশালে নিবাস গাড়েন। সর্বানন্দ দাশগুপ্ত জন্মসূত্রে হিন্দু ছিলেন; পরে ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষা নেন। তিনি বরিশালে ব্রাহ্ম সমাজ আন্দোলনের প্রাথমিক পর্যায়ে অংশগ্রহণ করেন এবং তাঁর মানবহিতৈষী কাজের জন্যে সমাদৃত ছিলেন। জীবনানন্দের পিতা সত্যানন্দ দাশগুপ্ত সর্বানন্দের দ্বিতীয় পুত্র। সত্যানন্দ দাশগুপ্ত (১৮৬৩-১৯৪২) ছিলেন বরিশাল ব্রজমোহন স্কুলের শিক্ষক, প্রাবন্ধিক, বরিশাল ব্রাহ্ম সমাজের সম্পাদক এবং ব্রাহ্মসমাজের মুখপত্র ব্রাহ্মবাদী পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদক।
জীবনানন্দের মাতা কুসুমকুমারী দাশ ছিলেন কবি, তাঁর সুপরিচিত কবিতা আদর্শ ছেলে (আমাদের দেশে হবে সেই ছেলে কবে/ কথায় না বড় হয়ে কাজে বড়ো হবে) আজও শিশুশ্রেণীর পাঠ্য। জীবনানন্দ ছিলেন পিতামাতার জ্যেষ্ঠ সন্তান; তার ডাকনাম ছিল মিলু। তার ভাই অশোকানন্দ দাশ ১৯০৮ খ্রিস্টাব্দে এবং বোন সুচরিতা দাশ ১৯১৫ খ্রিস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা কম বয়সে স্কুলে ভর্তি হওয়ার বিরোধী ছিলেন ব’লে বাড়িতে মায়ের কাছেই মিলুর বাল্যশিক্ষার সূত্রপাত। ভোরে ঘুম থেকে উঠেই পিতার কণ্ঠে উপনিষদ আবৃত্তি ও মায়ের গান শুনতেন। লাজুক স্বভাবের হলেও তার খেলাধুলা, ভ্রমণ ও সাঁতারের অভ্যাস ছিল। ছেলেবেলায় একবার কঠিন অসুখে পড়েন। স্বাস্থ্য উদ্ধারের জন্যে মাতা ও মাতামহ হাসির গানের কবি চন্দ্রনাথের সাথে লক্ষ্মৌ, আগ্রা, দিল্লী প্রভৃতি স্থান ভ্রমণ করেন।
১৯০৮ খ্রিস্টাব্দের জানুয়ারিতে আট বছরের মিলুকে ব্রজমোহন স্কুলে পঞ্চম শ্রেণীতে ভর্তি করানো হয়। স্কুলে থাকাকালীন সময়েই তার বাংলা ও ইংরেজিতে রচনার সূচনা হয়, এ ছাড়াও ছবি আঁকার দিকেও তার ঝোঁক ছিল। ১৯১৫ সালে তিনি ব্রজমোহন বিদ্যালয় থেকে প্রথম বিভাগসহ ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করেন। দু’বছর পর ব্রজমোহন কলেজ থেকে ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষায় পূর্বের ফলাফলের পুনরাবৃত্তি ঘটান ; অতঃপর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হবার উদ্দেশ্যে বরিশাল ত্যাগ করেন।
কলকাতা জীবন: জীবনানন্দ কলকাতার নামকরা প্রেসিডেন্সি কলেজে ভর্তি হন। ১৯১৯ খ্রিস্টাব্দে তিনি এ কলেজ থেকে ইংরেজিতে অনার্সসহ বি.এ. পাশ করেন। ওই বছরেই ব্রাহ্মবাদী পত্রিকার বৈশাখ সংখ্যায় তার প্রথম কবিতা ছাপা হয়। কবিতাটির নাম ছিল বর্ষ আবাহন। কবিতাটিতে কবির নাম ছাপা হয়নি, কেবল সম্মানসূচক শ্রী কথাটি লেখা ছিল। তবে পত্রিকার বর্ষশেষের নির্ঘণ্ট সূচিতে তার পূর্ণ নাম ছাপা হয়: শ্রী জীবনানন্দ দাশগুপ্ত, বিএ। ১৯২১ খ্রিস্টাব্দে তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হতে দ্বিতীয় বিভাগসহ মাস্টার্স ডিগ্রি অর্জন করেন। তিনি কিছুকাল আইনশাস্ত্রেও অধ্যয়ন করেন। সে সময়ে তিনি হ্যারিসন রোডের প্রেসিডেন্সি বোর্ডিংয়ে থাকতেন। তবে পরীক্ষার ঠিক আগেই তিনি ব্যাসিলারি ডায়রিয়ায় আক্রান্ত হন, যা তার প্রস্তুতি বাঁধাগ্রস্ত করে। ১৯২২ খ্রিস্টাব্দে জীবনানন্দ কলকাতা সিটি কলেজে অধ্যাপনা শুরু করেন এবং আইনশাস্ত্র অধ্যয়ন ছেড়ে দেন।
কর্মজীবন : অধ্যাপনার কাজে তাঁর কর্মজীবনের সূচনা ও সমাপ্তি। এমএ পাসের পর কলকাতায় কলেজের বোর্ডিংয়ে থাকার প্রয়োজন হলে তিনি আইন পড়া শুরু করেন। এ সময় তিনি ১৯২২ খ্রিস্টাব্দে কলকাতার ব্রাহ্মসমাজ পরিচালিত সিটি কলেজে টিউটর হিসেবে শিক্ষকতা শুরু করেন। ১৯২৮-এ সরস্বতী পূজা নিয়ে গোলযোগ শুরু হলে অন্যান্য কয়েকজন শিক্ষকের সঙ্গে তাঁকেও ছাঁটাই করে কলেজ কর্তৃপক্ষ। জীবনের শেষভাগে কিছুদিনের জন্য কলকাতার একটি দৈনিক পত্রিকা স্বরাজ-এর সাহিত্য বিভাগের সম্পাদনায় নিযুক্ত ছিলেন। অধ্যাপনা করেছেন বর্তমান বাংলাদেশ ও ভারতের অনেকগুলো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে, যার মধ্যে আছে সিটি কলেজ, কলকাতা (১৯২২-১৯২৮), বাগেরহাট কলেজ, খুলনা (১৯২৯); রামযশ কলেজ, দিল্লী (১৯৩০-১৯৩১), ব্রজমোহন কলেজ, বরিশাল (১৯৩৫-১৯৪৮), খড়গপুর কলেজ (১৯৫১-১৯৫২), বড়িশা কলেজ (অধুনা ‘বিবেকানন্দ কলেজ’ কলকাতা) (১৯৫৩) এবং হাওড়া গার্লস কলেজ, কলকাতা, (১৯৫৩-১৯৫৪)। তার কর্মজীবন আদৌ মসৃণ ছিল না। চাকুরী তথা জীবিকার অভাব তাকে আমৃত্যু কষ্ট দিয়েছে। একটি চাকুরির জন্য হন্যে হয়ে তিনি দ্বারে দ্বারে ঘুরেছেন। স্ত্রী লাবণ্য দাশ স্কুলে শিক্ষকতা করে জীবিকার অভাব কিছুটা পুষিয়েছেন। ১৯৫৪ সালে অকাল মৃত্যুর সময় তিনি হাওড়া গার্লস কলেজ কর্মরত ছিলেন। দুই দফা দীর্ঘ বেকার জীবনে তিনি ইন্সুরেন্স কোম্পানীর এজেন্ট হিসাবে কাজ করেছেন এবং প্রধানত গৃহশিক্ষকতা করে সংসার চালিয়েছেন। এছাড়া ব্যবসার চেষ্টাও করেছিলেন বছরখানেক। দারিদ্র্য এবং অনটন ছিল তার কর্মজীবনের ছায়াসঙ্গী।
 সাহিত্যিক জীবন : সম্ভবতঃ মা কুসুম কুমারী দাশের প্রভাবেই ছেলে বেলায় পদ্য লিখতে শুরু করেন তিনি। ১৯১৯ সালে তাঁর লেখা একটি কবিতা প্রকাশিত হয়। এটিই তাঁর প্রথম প্রকাশিত কবিতা। কবিতাটির নাম বর্ষা আবাহন। এটি ব্রহ্মবাদী পত্রিকার ১৩২৬ সনের বৈশাখ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল। তখন তিনি শ্রী জীবনানন্দ দাশগুপ্ত নামে লিখতেন। ১৯২৭ সাল থেকে তিনি জীবনানন্দ দাশ নামে লিখতে শুরু করেন। ১৬ জুন ১৯২৫ দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ এর লোকান্তর হলে তিনি ‘দেশবন্ধুর প্রয়াণে’ শিরোনামে একটি কবিতা লিখেছিলেন যা বংগবাণী পত্রিকার ১৩৩২ সনের শ্রাবণ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। তবে দীনেশরঞ্জন দাস সম্পাদিত কল্লোল পত্রিকায় ১৩৩২ (১৯২৬ খ্রি.) ফাল্গুন সংখ্যায় তাঁর নীলিমা শীর্ষক কবিতাটি প্রকাশিত হলে আধুনিক বাংলা কবিতার ভুবনে তার অন্নপ্রাশন হয়। জীবদ্দশায় তাঁর ৭টি কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয়। প্রথম প্রকাশিত ঝরাপালক শীর্ষক কাব্যগ্রন্থে তাঁর প্রকৃত কবিত্বশক্তি ফুটে ওঠেনি, বরং এতে কবি কাজী নজরুল ইসলাম, মোহিতলাল মজুমদার ও সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের প্রকট প্রভাব প্রত্যক্ষ হয়। তবে দ্রুত তিনি স্বকীয়তা অর্জন করেছিলেন। দীর্ঘ ব্যবধানে প্রকাশিত দ্বিতীয় কাব্য সংকলন ধূসর পাণ্ডুলিপি-তে তাঁর স্বকীয় কাব্য কৌশল পরিস্ফূট হয়ে ওঠে। বাংলা সাহিত্যের ভুবনে তাঁর বৈশিষ্ট্যগুলো আলোচনার বিষয় হয়ে ওঠে। শেষের দিককার কবিতায় অর্থ নির্মলতার অভাব ছিল। সাতটি তারার তিমির প্রকাশিত হওয়ার পর তার বিরুদ্ধে দুবোর্ধ্যতার অভিযোগ ওঠে। নিজ কবিতার অবমূল্যায়ন নিয়ে জীবনানন্দ খুব ভাবিত ছিলেন। তিনি নিজেই স্বীয় রচনার অর্থায়ন করার অভিপ্রায় ব্যক্ত করেছিলেন যদিও শেষাবধি তা সম্ভব হয়ে ওঠেনি। তবে কবি নিজেই নিজ রচনার কড়া সমালোচক ছিলেন। তাই সাড়ে আট শত কবিতার বেশী কবিতা লিখলেও তিনি জীবদ্দশায় মাত্র ২৬২টি কবিতা বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় ও কাব্যসংকলনে প্রকাশ করতে দিয়েছিলেন। এমনকি রূপসী বাংলার সম্পূর্ণ প্রস্তুত পাণ্ডুলিপি তোরঙ্গে মজুদ থাকলেও তা প্রকাশের সিদ্ধান্ত নিতে পারেননি জীবনানন্দ দাশ। তবে তিনি এ কাব্যগ্রন্থটির নাম দিয়েছিলেন বাংলার ত্রস্ত নীলিমা যা তার মৃত্যুর পর আবিষ্কৃত এবং রূপসী বাংলা প্রচ্ছদনামে প্রকাশিত হয়। আরেকটি পাণ্ডুলিপি আবিষ্কৃত হয় মৃত্যু পরবর্তীকালে যা বেলা অবেলা কালবেলা নামে প্রকাশিত হয়। জীবদ্দশায় তার একমাত্র পরিচয় ছিল কবি। অর্থের প্রয়োজনে তিনি কিছু প্রবন্ধ লিখেছিলেন ও প্রকাশ করেছিলেন। তবে নিভৃতে গল্প এবং উপন্যাস লিখেছিলেন প্রচুর যার একটিও প্রকাশের ব্যবস্থা নেননি। এছাড়া ষাট-পয়ষটিট্টিরও বেশি খাতায় “লিটেরেরী নোটস” লিখেছিলেন যার অধিকাংশ এখনও প্রকাশিত হয়নি।
সাহিত্যিক জীবন : সম্ভবতঃ মা কুসুম কুমারী দাশের প্রভাবেই ছেলে বেলায় পদ্য লিখতে শুরু করেন তিনি। ১৯১৯ সালে তাঁর লেখা একটি কবিতা প্রকাশিত হয়। এটিই তাঁর প্রথম প্রকাশিত কবিতা। কবিতাটির নাম বর্ষা আবাহন। এটি ব্রহ্মবাদী পত্রিকার ১৩২৬ সনের বৈশাখ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল। তখন তিনি শ্রী জীবনানন্দ দাশগুপ্ত নামে লিখতেন। ১৯২৭ সাল থেকে তিনি জীবনানন্দ দাশ নামে লিখতে শুরু করেন। ১৬ জুন ১৯২৫ দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ এর লোকান্তর হলে তিনি ‘দেশবন্ধুর প্রয়াণে’ শিরোনামে একটি কবিতা লিখেছিলেন যা বংগবাণী পত্রিকার ১৩৩২ সনের শ্রাবণ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। তবে দীনেশরঞ্জন দাস সম্পাদিত কল্লোল পত্রিকায় ১৩৩২ (১৯২৬ খ্রি.) ফাল্গুন সংখ্যায় তাঁর নীলিমা শীর্ষক কবিতাটি প্রকাশিত হলে আধুনিক বাংলা কবিতার ভুবনে তার অন্নপ্রাশন হয়। জীবদ্দশায় তাঁর ৭টি কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয়। প্রথম প্রকাশিত ঝরাপালক শীর্ষক কাব্যগ্রন্থে তাঁর প্রকৃত কবিত্বশক্তি ফুটে ওঠেনি, বরং এতে কবি কাজী নজরুল ইসলাম, মোহিতলাল মজুমদার ও সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের প্রকট প্রভাব প্রত্যক্ষ হয়। তবে দ্রুত তিনি স্বকীয়তা অর্জন করেছিলেন। দীর্ঘ ব্যবধানে প্রকাশিত দ্বিতীয় কাব্য সংকলন ধূসর পাণ্ডুলিপি-তে তাঁর স্বকীয় কাব্য কৌশল পরিস্ফূট হয়ে ওঠে। বাংলা সাহিত্যের ভুবনে তাঁর বৈশিষ্ট্যগুলো আলোচনার বিষয় হয়ে ওঠে। শেষের দিককার কবিতায় অর্থ নির্মলতার অভাব ছিল। সাতটি তারার তিমির প্রকাশিত হওয়ার পর তার বিরুদ্ধে দুবোর্ধ্যতার অভিযোগ ওঠে। নিজ কবিতার অবমূল্যায়ন নিয়ে জীবনানন্দ খুব ভাবিত ছিলেন। তিনি নিজেই স্বীয় রচনার অর্থায়ন করার অভিপ্রায় ব্যক্ত করেছিলেন যদিও শেষাবধি তা সম্ভব হয়ে ওঠেনি। তবে কবি নিজেই নিজ রচনার কড়া সমালোচক ছিলেন। তাই সাড়ে আট শত কবিতার বেশী কবিতা লিখলেও তিনি জীবদ্দশায় মাত্র ২৬২টি কবিতা বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় ও কাব্যসংকলনে প্রকাশ করতে দিয়েছিলেন। এমনকি রূপসী বাংলার সম্পূর্ণ প্রস্তুত পাণ্ডুলিপি তোরঙ্গে মজুদ থাকলেও তা প্রকাশের সিদ্ধান্ত নিতে পারেননি জীবনানন্দ দাশ। তবে তিনি এ কাব্যগ্রন্থটির নাম দিয়েছিলেন বাংলার ত্রস্ত নীলিমা যা তার মৃত্যুর পর আবিষ্কৃত এবং রূপসী বাংলা প্রচ্ছদনামে প্রকাশিত হয়। আরেকটি পাণ্ডুলিপি আবিষ্কৃত হয় মৃত্যু পরবর্তীকালে যা বেলা অবেলা কালবেলা নামে প্রকাশিত হয়। জীবদ্দশায় তার একমাত্র পরিচয় ছিল কবি। অর্থের প্রয়োজনে তিনি কিছু প্রবন্ধ লিখেছিলেন ও প্রকাশ করেছিলেন। তবে নিভৃতে গল্প এবং উপন্যাস লিখেছিলেন প্রচুর যার একটিও প্রকাশের ব্যবস্থা নেননি। এছাড়া ষাট-পয়ষটিট্টিরও বেশি খাতায় “লিটেরেরী নোটস” লিখেছিলেন যার অধিকাংশ এখনও প্রকাশিত হয়নি।
 স্বীকৃতি ও সমালোচনা এবং পুরস্কার : জীবদ্দশায় অসাধারণ কবি হিসেবে পরিচিতি থাকলেও তিনি খ্যাতি অর্জন করে উঠতে পারেননি। এর জন্য তার প্রচারবিমুখতাও দায়ী; তিনি ছিলেন বিবরবাসী মানুষ। তবে মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই তিনি বাংলা ভাষায় আধুনিক কবিতার পথিকৃতদের একজন হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছেন। জীবনানন্দ দাশের জীবন এবং কবিতার উপর প্রচুর গ্রন্থ লেখা হয়েছে এবং এখনো হচ্ছে, বাংলা ভাষায়। এর বাইরে ইংরেজিতে তার ওপর লিখেছেন ক্লিনটন বি সিলি, আ পোয়েট আর্পাট নামের একটি গ্রন্থে। ইংরেজি ছাড়াও ফরাসিসহ কয়েকটি ইউরোপীয় ভাষায় তাঁর কবিতা অনূদিত হয়েছে। তিনি যদিও কবি হিসেবেই সমধিক পরিচিত কিন্তু মৃত্যুর পর থেকে ২০০৯ খ্রিস্টাব্দ অবধি তাঁর যে বিপুল পাণ্ডুলিপিরাশি উদ্ঘাটিত হয়েছে তার মধ্যে উপন্যাসের সংখ্যা ১৪ এবং গল্পের সংখ্যা শতাধিক।
স্বীকৃতি ও সমালোচনা এবং পুরস্কার : জীবদ্দশায় অসাধারণ কবি হিসেবে পরিচিতি থাকলেও তিনি খ্যাতি অর্জন করে উঠতে পারেননি। এর জন্য তার প্রচারবিমুখতাও দায়ী; তিনি ছিলেন বিবরবাসী মানুষ। তবে মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই তিনি বাংলা ভাষায় আধুনিক কবিতার পথিকৃতদের একজন হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছেন। জীবনানন্দ দাশের জীবন এবং কবিতার উপর প্রচুর গ্রন্থ লেখা হয়েছে এবং এখনো হচ্ছে, বাংলা ভাষায়। এর বাইরে ইংরেজিতে তার ওপর লিখেছেন ক্লিনটন বি সিলি, আ পোয়েট আর্পাট নামের একটি গ্রন্থে। ইংরেজি ছাড়াও ফরাসিসহ কয়েকটি ইউরোপীয় ভাষায় তাঁর কবিতা অনূদিত হয়েছে। তিনি যদিও কবি হিসেবেই সমধিক পরিচিত কিন্তু মৃত্যুর পর থেকে ২০০৯ খ্রিস্টাব্দ অবধি তাঁর যে বিপুল পাণ্ডুলিপিরাশি উদ্ঘাটিত হয়েছে তার মধ্যে উপন্যাসের সংখ্যা ১৪ এবং গল্পের সংখ্যা শতাধিক।
নিখিলবঙ্গ রবীন্দ্রসাহিত্য সম্মেলন ১৯৫২ খৃস্টাব্দে পরিবর্ধিত সিগনেট সংস্করণ বনলতা সেন কাব্যগ্রন্থটি বাংলা ১৩৫৯-এর শ্রেষ্ঠ কাব্যগ্রন্থ বিবেচনায় পুরস্কৃত করা হয়। কবির মৃত্যুর পর ১৯৫৫ খৃস্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে জীবনানন্দ দাশের শ্রেষ্ঠ কবিতা (১৯৫৪) সাহিত্য অকাদেমি পুরস্কার লাভ করে।
 মৃত্যু : ১৪ই অক্টোবর, ১৯৫৪ তারিখে কোলকাতার বালিগঞ্জে এক ট্রাম দুর্ঘটনায় তিনি আহত হন। ট্রামের ক্যাচারে আটকে তার শরীর দলিত হয়ে গিয়েছিল। ভেঙ্গে গিয়েছিল কণ্ঠা, ঊরু এবং পাঁজরের হাড়। গুরুতরভাবে আহত জীবনানন্দের চিৎকার শুনে ছুটে এসে নিকটস্থ চায়ের দোকানের মালিক চূণীলাল এবং অন্যান্যরা তাঁকে উদ্ধার করে। তাঁকে ভর্তি করা হয় শম্ভূনাথ পণ্ডিত হাসপাতালে। এ সময় ডাঃ ভূমেন্দ্র গুহ-সহ অনেক তরুণ কবি জীবনানন্দের সুচিকিৎসার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করেছিলেন। কবি-সাহিত্যিক সজনীকান্ত দাস এ ব্যাপারে বিশেষ উদ্যোগ নিয়েছিলেন। তাঁর অনুরোধেই পশ্চিমবঙ্গের তদানীন্তন মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় কবিকে দেখতে এসেছিলেন এবং আহত কবির সুচিকিৎসার নির্দেশ দিয়েছিলেন যদিও এতে চিকিৎসার তেমন উন্নতি কিছু হয়নি। এ সময় স্ত্রী লাবণ্য দাশকে কদাচিৎ কাছে দেখা যায়। তিনি টালিগঞ্জে সিনেমার কাজে ব্যস্ত ছিলেন। জীবনানন্দের অবস্থা ক্রমশঃ জটিল হতে থাকে। শেষ পর্যন্ত নিউমোনিয়ায় আক্রান্ত হয়ে পড়েন কবি। চিকিৎসক ও সেবিকাদের সকল প্রচেষ্টা বিফলে দিয়ে ২২শে অক্টোবর, ১৯৫৪ তারিখে রাত্রি ১১টা ৩৫ মিনিটে কলকাতার শম্ভুনাথ পণ্ডিত হাসপাতালে তাঁর মৃত্যু হয়। আবদুল মান্নান সৈয়দ-সহ কেউ কেউ ধারণা করেছেন হয় আত্মহত্যা স্পৃহা ছিল দুর্ঘটনার মূল কারণ। জীবনানন্দ গবেষক ডাঃ ভূমেন্দ্র গুহ মনে করেন জাগতিক নিঃসহায়তা কবিকে মানসিকভাবে কাবু করেছিল এবং তাঁর জীবন স্পৃহা শূন্য করে দিয়েছিল। মৃত্যুচিন্তা কবির মাথায় দানা বেঁধেছিল। তিনি প্রায়ই ট্রাম দুর্ঘটনায় মৃত্যুর কথা ভাবতেন। গত এক শত বৎসরে ট্রাম দুর্ঘটনায় কোলকাতায় মৃত্যুর সংখ্যা মাত্র একটি। তিনি আর কেউ নন, কবি জীবনানন্দ দাশ। কিন্তু প্রত্যক্ষদর্শীর মতে এ সময় দুই হাতে দুই থোকা ডাব নিয়ে ট্রাম লাইন পার হচ্ছিলেন কবি। আত্মহননের সিদ্ধান্ত নিয়ে দুই হাতে দুই থোকা ডাব নিয়ে গৃহে ফেরার সড়কে ওঠার জন্য ট্রাম লাইন পারি দেয়া খুব গ্রহণযোগ্য যুক্তি নয়।
মৃত্যু : ১৪ই অক্টোবর, ১৯৫৪ তারিখে কোলকাতার বালিগঞ্জে এক ট্রাম দুর্ঘটনায় তিনি আহত হন। ট্রামের ক্যাচারে আটকে তার শরীর দলিত হয়ে গিয়েছিল। ভেঙ্গে গিয়েছিল কণ্ঠা, ঊরু এবং পাঁজরের হাড়। গুরুতরভাবে আহত জীবনানন্দের চিৎকার শুনে ছুটে এসে নিকটস্থ চায়ের দোকানের মালিক চূণীলাল এবং অন্যান্যরা তাঁকে উদ্ধার করে। তাঁকে ভর্তি করা হয় শম্ভূনাথ পণ্ডিত হাসপাতালে। এ সময় ডাঃ ভূমেন্দ্র গুহ-সহ অনেক তরুণ কবি জীবনানন্দের সুচিকিৎসার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করেছিলেন। কবি-সাহিত্যিক সজনীকান্ত দাস এ ব্যাপারে বিশেষ উদ্যোগ নিয়েছিলেন। তাঁর অনুরোধেই পশ্চিমবঙ্গের তদানীন্তন মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় কবিকে দেখতে এসেছিলেন এবং আহত কবির সুচিকিৎসার নির্দেশ দিয়েছিলেন যদিও এতে চিকিৎসার তেমন উন্নতি কিছু হয়নি। এ সময় স্ত্রী লাবণ্য দাশকে কদাচিৎ কাছে দেখা যায়। তিনি টালিগঞ্জে সিনেমার কাজে ব্যস্ত ছিলেন। জীবনানন্দের অবস্থা ক্রমশঃ জটিল হতে থাকে। শেষ পর্যন্ত নিউমোনিয়ায় আক্রান্ত হয়ে পড়েন কবি। চিকিৎসক ও সেবিকাদের সকল প্রচেষ্টা বিফলে দিয়ে ২২শে অক্টোবর, ১৯৫৪ তারিখে রাত্রি ১১টা ৩৫ মিনিটে কলকাতার শম্ভুনাথ পণ্ডিত হাসপাতালে তাঁর মৃত্যু হয়। আবদুল মান্নান সৈয়দ-সহ কেউ কেউ ধারণা করেছেন হয় আত্মহত্যা স্পৃহা ছিল দুর্ঘটনার মূল কারণ। জীবনানন্দ গবেষক ডাঃ ভূমেন্দ্র গুহ মনে করেন জাগতিক নিঃসহায়তা কবিকে মানসিকভাবে কাবু করেছিল এবং তাঁর জীবন স্পৃহা শূন্য করে দিয়েছিল। মৃত্যুচিন্তা কবির মাথায় দানা বেঁধেছিল। তিনি প্রায়ই ট্রাম দুর্ঘটনায় মৃত্যুর কথা ভাবতেন। গত এক শত বৎসরে ট্রাম দুর্ঘটনায় কোলকাতায় মৃত্যুর সংখ্যা মাত্র একটি। তিনি আর কেউ নন, কবি জীবনানন্দ দাশ। কিন্তু প্রত্যক্ষদর্শীর মতে এ সময় দুই হাতে দুই থোকা ডাব নিয়ে ট্রাম লাইন পার হচ্ছিলেন কবি। আত্মহননের সিদ্ধান্ত নিয়ে দুই হাতে দুই থোকা ডাব নিয়ে গৃহে ফেরার সড়কে ওঠার জন্য ট্রাম লাইন পারি দেয়া খুব গ্রহণযোগ্য যুক্তি নয়।
 কাব্যগ্রন্থ : জীবনানন্দের কাব্য গ্রন্থ সমূহের প্রকাশকাল সম্পর্কে বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য যে, কয়েকটি কাব্যগ্রন্থের একাধিক পরিবর্ধিত সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছিল। কেবল প্রথম প্রকাশনার বৎসর উল্লিখিত। মৃত্যু পরবর্তী প্রকাশিত গ্রন্থসমূহ তারকা চিহ্নিত। ঝরা পালক (১৯২৭)। ধূসর পাণ্ডুলিপি (১৯৩৬)। বনলতা সেন (১৯৪২, কবিতাভবন সংস্করণ)। মহাপৃথিবী (১৯৪৪)। সাতটি তারার তিমির (১৯৪৮)। বনলতা সেন (১৯৫২, সিগনেট প্রেস সংস্করণ)। জীবনানন্দ দাশের শ্রেষ্ঠ কবিতা (১৯৫৪)। রূপসী বাংলা (১৯৫৭)*। বেলা অবেলা কালবেলা (১৯৬১)*। সুদর্শনা (১৯৭৪)*। আলো পৃথিবী (১৯৮১) *। মনোবিহঙ্গম*। অপ্রকাশিত একান্ন (১৯৯৯) * প্রবন্ধগ্রন্থ কবিতার কথা (১৯৫৫)। জীবনানন্দ দাশের প্রবন্ধ সমগ্র (১৯৯০, সম্পাদকঃ ফয়জুল লতিফ চৌধুরী)*। উপন্যাস
কাব্যগ্রন্থ : জীবনানন্দের কাব্য গ্রন্থ সমূহের প্রকাশকাল সম্পর্কে বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য যে, কয়েকটি কাব্যগ্রন্থের একাধিক পরিবর্ধিত সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছিল। কেবল প্রথম প্রকাশনার বৎসর উল্লিখিত। মৃত্যু পরবর্তী প্রকাশিত গ্রন্থসমূহ তারকা চিহ্নিত। ঝরা পালক (১৯২৭)। ধূসর পাণ্ডুলিপি (১৯৩৬)। বনলতা সেন (১৯৪২, কবিতাভবন সংস্করণ)। মহাপৃথিবী (১৯৪৪)। সাতটি তারার তিমির (১৯৪৮)। বনলতা সেন (১৯৫২, সিগনেট প্রেস সংস্করণ)। জীবনানন্দ দাশের শ্রেষ্ঠ কবিতা (১৯৫৪)। রূপসী বাংলা (১৯৫৭)*। বেলা অবেলা কালবেলা (১৯৬১)*। সুদর্শনা (১৯৭৪)*। আলো পৃথিবী (১৯৮১) *। মনোবিহঙ্গম*। অপ্রকাশিত একান্ন (১৯৯৯) * প্রবন্ধগ্রন্থ কবিতার কথা (১৯৫৫)। জীবনানন্দ দাশের প্রবন্ধ সমগ্র (১৯৯০, সম্পাদকঃ ফয়জুল লতিফ চৌধুরী)*। উপন্যাস
মাল্যবান (১৯৭৩)*। সুতীর্থ (১৯৭৭)। চারজন (২০০৪: সম্পাদকঃ ভূমেন্দ্র গুহ ও ফয়সাল শাহরিয়ার)*। গল্পগ্রন্থ জীবনানন্দ দাশের গল্প (১৯৭২, সম্পাদনা: সুকুমার ঘোষ ও সুবিনয় মুস্তাফী)। জীবনানন্দ দাশের শ্রেষ্ঠ গল্প (১৯৮৯, সম্পাদনা: আবদুল মান্নান সৈয়দ)। পত্রসংকলন জীবনানন্দ দাশের পত্রাবলী (বাংলা ১৩৮৫, সম্পাদকঃ দীপেনকুমার রায়)। জীবনানন্দ দাশের পত্রাবলী (১৯৮৬, সম্পাদকঃ আবদুল মান্নান সৈয়দ) )

প্রিয় কবি’র বিখ্যাত একটি কবিতা ::
বনলতা সেন
হাজার বছর ধরে আমি পথ হাঁটিতেছি পৃথিবীর পথে,
সিংহল সমুদ্র থেকে নিশীথের অন্ধকারে মালয় সাগরে
অনেক ঘুরেছি আমি; বিম্বিসার অশোকের ধূসর জগতে
সেখানে ছিলাম আমি; আরো দূর অন্ধকার বিদর্ভ নগরে;
আমি ক্লান্ত প্রাণ এক, চারিদিকে জীবনের সমুদ্র সফেন,
আমারে দুদণ্ড শান্তি দিয়েছিল নাটোরের বনলতা সেন।
চুল তার কবেকার অন্ধকার বিদিশার নিশা,
মুখ তার শ্রাবস্তীর কারুকার্য; অতিদূর সমুদ্রের’পর
হাল ভেঙ্গে যে নাবিক হারায়েছে দিশা
সবুজ ঘাসের দেশ যখন সে চোখে দেখে দারুচিনি-দ্বীপের ভিতর,
তেমনই দেখেছি তারে অন্ধকারে; বলেছে সে, ‘এতোদিন কোথায় ছিলেন?’
পাখির নীড়ের মত চোখ তুলে চাওয়া নাটোরের বনলতা সেন।
সমস্ত দিনের শেষে শিশিরের শব্দের মতন
সন্ধ্যা আসে; ডানার রৌদ্রের গন্ধ মুছে ফেলে চিল;
পৃথিবীর সব রঙ মুছে গেলে পাণ্ডুলিপি করে আয়োজন,
তখন গল্পের তরে জোনাকির রঙে ঝিলমিল।
সব পাখি ঘরে আসে — সব নদী; ফুরায় এ-জীবনের সব লেনদেন;
থাকে শুধু অন্ধকার, মুখোমুখি বসিবার বনলতা সেন।
youtu.be/bmuJesgNvTs
কবি জীবনানন্দ দাশ এর প্রয়াণ দিবসে তাঁর প্রতি আমাদের শ্রদ্ধাঞ্জলি।
![]()
তথ্য সংগ্রহ : বাংলা উইকিপিডিয়া।
প্রদায়ক : পোস্টদাতা। পোস্টদাতার ফেসবুক লিঙ্ক : আজাদ কাশ্মীর জামান।
 যৌবন (১৮৭৮-১৯০১) ১৮৭৮ সালে ব্যারিস্টারি পড়ার উদ্দেশ্যে ইংল্যান্ডে যান রবীন্দ্রনাথ। প্রথমে তিনি ব্রাইটনের একটি পাবলিক স্কুলে ভর্তি হয়েছিলেন। ১৮৭৯ সালে ইউনিভার্সিটি কলেজ লন্ডনে আইন বিদ্যা নিয়ে পড়াশোনা শুরু করেন। কিন্তু সাহিত্যচর্চার আকর্ষণে সেই পড়াশোনা তিনি সমাপ্ত করতে পারেননি। ইংল্যান্ডে থাকাকালীন শেক্সপিয়ার ও অন্যান্য ইংরেজ সাহিত্যিকদের রচনার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের পরিচয় ঘটে। এই সময় তিনি বিশেষ মনোযোগ সহকারে পাঠ করেন রিলিজিও মেদিচি, কোরিওলেনাস এবং অ্যান্টনি অ্যান্ড ক্লিওপেট্রা। এই সময় তাঁর ইংল্যান্ড বাসের অভিজ্ঞতার কথা ভারতী পত্রিকায় পত্রাকারে পাঠাতেন রবীন্দ্রনাথ। পত্রিকায় এই লেখাগুলি জ্যেষ্ঠভ্রাতা দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সমালোচনাসহ প্রকাশিত হত য়ুরোপযাত্রী কোনো বঙ্গীয় যুবকের পত্রধারা নামে। ১৮৮১ সালে সেই পত্রাবলি য়ুরোপ-প্রবাসীর পত্র নামে গ্রন্থাকারে ছাপা হয়। এটিই ছিল রবীন্দ্রনাথের প্রথম গদ্যগ্রন্থ তথা প্রথম চলিত ভাষায় লেখা গ্রন্থ। শেষে ১৮৮০ সালে প্রায় দেড় বছর ইংল্যান্ডে কাটিয়ে কোনো ডিগ্রি না নিয়ে এবং ব্যারিস্টারি পড়া শুরু না করেই তিনি দেশে ফিরে আসেন।
যৌবন (১৮৭৮-১৯০১) ১৮৭৮ সালে ব্যারিস্টারি পড়ার উদ্দেশ্যে ইংল্যান্ডে যান রবীন্দ্রনাথ। প্রথমে তিনি ব্রাইটনের একটি পাবলিক স্কুলে ভর্তি হয়েছিলেন। ১৮৭৯ সালে ইউনিভার্সিটি কলেজ লন্ডনে আইন বিদ্যা নিয়ে পড়াশোনা শুরু করেন। কিন্তু সাহিত্যচর্চার আকর্ষণে সেই পড়াশোনা তিনি সমাপ্ত করতে পারেননি। ইংল্যান্ডে থাকাকালীন শেক্সপিয়ার ও অন্যান্য ইংরেজ সাহিত্যিকদের রচনার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের পরিচয় ঘটে। এই সময় তিনি বিশেষ মনোযোগ সহকারে পাঠ করেন রিলিজিও মেদিচি, কোরিওলেনাস এবং অ্যান্টনি অ্যান্ড ক্লিওপেট্রা। এই সময় তাঁর ইংল্যান্ড বাসের অভিজ্ঞতার কথা ভারতী পত্রিকায় পত্রাকারে পাঠাতেন রবীন্দ্রনাথ। পত্রিকায় এই লেখাগুলি জ্যেষ্ঠভ্রাতা দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সমালোচনাসহ প্রকাশিত হত য়ুরোপযাত্রী কোনো বঙ্গীয় যুবকের পত্রধারা নামে। ১৮৮১ সালে সেই পত্রাবলি য়ুরোপ-প্রবাসীর পত্র নামে গ্রন্থাকারে ছাপা হয়। এটিই ছিল রবীন্দ্রনাথের প্রথম গদ্যগ্রন্থ তথা প্রথম চলিত ভাষায় লেখা গ্রন্থ। শেষে ১৮৮০ সালে প্রায় দেড় বছর ইংল্যান্ডে কাটিয়ে কোনো ডিগ্রি না নিয়ে এবং ব্যারিস্টারি পড়া শুরু না করেই তিনি দেশে ফিরে আসেন। ১৮৯১ সাল থেকে পিতার আদেশে নদিয়া (নদিয়ার উক্ত অংশটি অধুনা বাংলাদেশের কুষ্টিয়া জেলা), পাবনা ও রাজশাহী জেলা এবং উড়িষ্যার জমিদারির তদারকি শুরু করেন রবীন্দ্রনাথ। কুষ্টিয়ার শিলাইদহের কুঠিবাড়িতে রবীন্দ্রনাথ দীর্ঘ সময় অতিবাহিত করেছিলেন। জমিদার রবীন্দ্রনাথ শিলাইদহে “পদ্মা” নামে একটি বিলাসবহুল পারিবারিক বজরায় চড়ে প্রজাবর্গের কাছে খাজনা আদায় ও আশীর্বাদ প্রার্থনা করতে যেতেন। গ্রামবাসীরাও তাঁর সম্মানে ভোজসভার আয়োজন করতো।
১৮৯১ সাল থেকে পিতার আদেশে নদিয়া (নদিয়ার উক্ত অংশটি অধুনা বাংলাদেশের কুষ্টিয়া জেলা), পাবনা ও রাজশাহী জেলা এবং উড়িষ্যার জমিদারির তদারকি শুরু করেন রবীন্দ্রনাথ। কুষ্টিয়ার শিলাইদহের কুঠিবাড়িতে রবীন্দ্রনাথ দীর্ঘ সময় অতিবাহিত করেছিলেন। জমিদার রবীন্দ্রনাথ শিলাইদহে “পদ্মা” নামে একটি বিলাসবহুল পারিবারিক বজরায় চড়ে প্রজাবর্গের কাছে খাজনা আদায় ও আশীর্বাদ প্রার্থনা করতে যেতেন। গ্রামবাসীরাও তাঁর সম্মানে ভোজসভার আয়োজন করতো। ১৯০১ সালে রবীন্দ্রনাথ সপরিবারে শিলাইদহ ছেড়ে চলে আসেন বীরভূম জেলার বোলপুর শহরের উপকণ্ঠে শান্তিনিকেতনে। এখানে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৮৮৮ সালে একটি আশ্রম ও ১৮৯১ সালে একটি ব্রহ্মমন্দির প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। আশ্রমের আম্রকুঞ্জ উদ্যানে একটি গ্রন্থাগার নিয়ে রবীন্দ্রনাথ চালু করলেন ‘ব্রহ্মবিদ্যালয়’ বা ‘ব্রহ্মচর্যাশ্রম’ নামে একটি পরীক্ষামূলক স্কুল। ১৯০২ সালের ২৩ সেপ্টেম্বর মাত্র ত্রিশ বছর বয়সে কবিপত্নী মৃণালিনী দেবী মারা যান। ১৯০৩ সালের ১৯ সেপ্টেম্বর কন্যা রেণুকা, ১৯০৫ সালের ১৯ জানুয়ারি পিতা দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও ১৯০৭ সালের ২৩ নভেম্বর কনিষ্ঠ পুত্র শমীন্দ্রনাথের মৃত্যু হয়।
১৯০১ সালে রবীন্দ্রনাথ সপরিবারে শিলাইদহ ছেড়ে চলে আসেন বীরভূম জেলার বোলপুর শহরের উপকণ্ঠে শান্তিনিকেতনে। এখানে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৮৮৮ সালে একটি আশ্রম ও ১৮৯১ সালে একটি ব্রহ্মমন্দির প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। আশ্রমের আম্রকুঞ্জ উদ্যানে একটি গ্রন্থাগার নিয়ে রবীন্দ্রনাথ চালু করলেন ‘ব্রহ্মবিদ্যালয়’ বা ‘ব্রহ্মচর্যাশ্রম’ নামে একটি পরীক্ষামূলক স্কুল। ১৯০২ সালের ২৩ সেপ্টেম্বর মাত্র ত্রিশ বছর বয়সে কবিপত্নী মৃণালিনী দেবী মারা যান। ১৯০৩ সালের ১৯ সেপ্টেম্বর কন্যা রেণুকা, ১৯০৫ সালের ১৯ জানুয়ারি পিতা দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও ১৯০৭ সালের ২৩ নভেম্বর কনিষ্ঠ পুত্র শমীন্দ্রনাথের মৃত্যু হয়।


 আজ নাগরিক কবি শামসুর রাহমান এর ৭ম প্রয়াণ দিবস। শামসুর রাহমান বাংলাদেশ ও আধুনিক বাংলা সাহিত্যের অন্যতম প্রধান কবি। বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় ভাগে দুই বাংলায় তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব ও জনপ্রিয়তা প্রতিষ্ঠিত। তিনি একজন নাগরিক কবি ছিলেন। বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের ওপর লিখিত তাঁর দুটি কবিতা খুবই জনপ্রিয়। জন্ম : অক্টোবর ২৩, ১৯২৯। মৃত্যু : আগস্ট ১৭, ২০০৬। শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করি তার অমর কীর্তি। জানাই শ্রদ্ধাঞ্জলী।
আজ নাগরিক কবি শামসুর রাহমান এর ৭ম প্রয়াণ দিবস। শামসুর রাহমান বাংলাদেশ ও আধুনিক বাংলা সাহিত্যের অন্যতম প্রধান কবি। বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় ভাগে দুই বাংলায় তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব ও জনপ্রিয়তা প্রতিষ্ঠিত। তিনি একজন নাগরিক কবি ছিলেন। বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের ওপর লিখিত তাঁর দুটি কবিতা খুবই জনপ্রিয়। জন্ম : অক্টোবর ২৩, ১৯২৯। মৃত্যু : আগস্ট ১৭, ২০০৬। শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করি তার অমর কীর্তি। জানাই শ্রদ্ধাঞ্জলী। সাহিত্যধারা : বিংশ শতকের তিরিশের দশকের পাঁচ মহান কবির পর তিনিই আধুনিক বাংলা কবিতার প্রধান পুরুষ হিসেবে প্রসিদ্ধ। কেবল বাংলাদেশের কবি আল মাহমুদ এবং পশ্চিমবঙ্গের কবি শক্তি চট্টোপাধ্যায় বিংশ শতকের শেষার্ধে তুলনীয় কাব্যপ্রতিভার স্বাক্ষর রেখেছেন বলে ধারণা করা হয়। আধুনিক কবিতার সাথে পরিচয় ও আন্তর্জাতিক-আধুনিক চেতনার উন্মেষ ঘটে ১৯৪৯-এ, এবং তার প্রথম প্রকাশিত কবিতা ১৯৪৯ মুদ্রিত হয় সাপ্তাহিক সোনার বাংলা পত্রিকায়। শামসুর রাহমান বিভিন্ন পত্রিকায় সম্পাদকীয় ও উপসম্পাদকীয় লিখতে গিয়ে নানা ছন্দনাম নিয়েছেন তিনি যেগুলো হচ্ছে: সিন্দবাদ, চক্ষুষ্মান, লিপিকার, নেপথ্যে, জনান্তিকে, মৈনাক। পাকিস্তান সরকারের আমলে কলকাতার একটি সাহিত্য পত্রিকায় মজলুম আদিব (বিপন্ন লেখক) নামে কবিতা ছাপা হয় যা দিয়েছিলেন বাংলা সাহিত্যের বিশিষ্ট সমালোচক আবু সায়ীদ আইয়ুব। ব্যক্তিগত জীবন : ১৯৫৫ সালের ৮ই জুলাই শামসুর রাহমান জোহরা বেগমকে বিয়ে করেন। কবির তিন ছেলে ও দুই মেয়ে। তাদের নাম সুমায়রা আমিন, ফাইয়াজ রাহমান, ফাওজিয়া সাবেরিন, ওয়াহিদুর রাহমান মতিন ও শেবা রাহমান।
সাহিত্যধারা : বিংশ শতকের তিরিশের দশকের পাঁচ মহান কবির পর তিনিই আধুনিক বাংলা কবিতার প্রধান পুরুষ হিসেবে প্রসিদ্ধ। কেবল বাংলাদেশের কবি আল মাহমুদ এবং পশ্চিমবঙ্গের কবি শক্তি চট্টোপাধ্যায় বিংশ শতকের শেষার্ধে তুলনীয় কাব্যপ্রতিভার স্বাক্ষর রেখেছেন বলে ধারণা করা হয়। আধুনিক কবিতার সাথে পরিচয় ও আন্তর্জাতিক-আধুনিক চেতনার উন্মেষ ঘটে ১৯৪৯-এ, এবং তার প্রথম প্রকাশিত কবিতা ১৯৪৯ মুদ্রিত হয় সাপ্তাহিক সোনার বাংলা পত্রিকায়। শামসুর রাহমান বিভিন্ন পত্রিকায় সম্পাদকীয় ও উপসম্পাদকীয় লিখতে গিয়ে নানা ছন্দনাম নিয়েছেন তিনি যেগুলো হচ্ছে: সিন্দবাদ, চক্ষুষ্মান, লিপিকার, নেপথ্যে, জনান্তিকে, মৈনাক। পাকিস্তান সরকারের আমলে কলকাতার একটি সাহিত্য পত্রিকায় মজলুম আদিব (বিপন্ন লেখক) নামে কবিতা ছাপা হয় যা দিয়েছিলেন বাংলা সাহিত্যের বিশিষ্ট সমালোচক আবু সায়ীদ আইয়ুব। ব্যক্তিগত জীবন : ১৯৫৫ সালের ৮ই জুলাই শামসুর রাহমান জোহরা বেগমকে বিয়ে করেন। কবির তিন ছেলে ও দুই মেয়ে। তাদের নাম সুমায়রা আমিন, ফাইয়াজ রাহমান, ফাওজিয়া সাবেরিন, ওয়াহিদুর রাহমান মতিন ও শেবা রাহমান।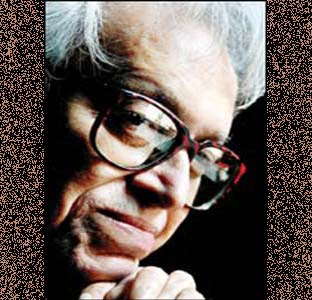 মৃত্যু : কবি শামসুর রাহমান ২০০৬ সালের ১৭ই আগস্ট বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা ৬ টা বেজে ৩৫ মিনিটে ঢাকায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ে চিকিৎসাধীন অবস্থায় শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তাঁর ইচ্ছানুযায়ী ঢাকাস্থ বনানী কবরস্থানে তাঁর মায়ের কবরে তাঁকে সমাধিস্থ করা হয়। জীবদ্দশায় তিনি পেয়েছেন অসংখ্য ভক্ত এবং মানুষের ভালোবাসা। পেয়েছেন আদমজী সাহিত্য পুরস্কার, বাংলা একাডেমী পুরস্কার, একুশে পদক, নাসির উদ্দিন স্বর্ণপদক, জীবনানন্দ পুরস্কার, আবুল মনসুর আহমেদ স্মৃতি পুরস্কার, মিতসুবিসি পুরস্কার (সাংবাদিকতার জন্য), স্বাধীনতা পদক এবং আনন্দ পুরস্কার। ভারতের যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় এবং রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় কবিকে সম্মান সূচক ডি.লিট উপাধিতে ভূষিত করে।
মৃত্যু : কবি শামসুর রাহমান ২০০৬ সালের ১৭ই আগস্ট বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা ৬ টা বেজে ৩৫ মিনিটে ঢাকায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ে চিকিৎসাধীন অবস্থায় শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তাঁর ইচ্ছানুযায়ী ঢাকাস্থ বনানী কবরস্থানে তাঁর মায়ের কবরে তাঁকে সমাধিস্থ করা হয়। জীবদ্দশায় তিনি পেয়েছেন অসংখ্য ভক্ত এবং মানুষের ভালোবাসা। পেয়েছেন আদমজী সাহিত্য পুরস্কার, বাংলা একাডেমী পুরস্কার, একুশে পদক, নাসির উদ্দিন স্বর্ণপদক, জীবনানন্দ পুরস্কার, আবুল মনসুর আহমেদ স্মৃতি পুরস্কার, মিতসুবিসি পুরস্কার (সাংবাদিকতার জন্য), স্বাধীনতা পদক এবং আনন্দ পুরস্কার। ভারতের যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় এবং রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় কবিকে সম্মান সূচক ডি.লিট উপাধিতে ভূষিত করে।
 জনগণের কবি সুকান্তের সমাজ-সচেতনতা, দৃষ্টিভঙ্গি ও সাহসী কলমে তাঁর শক্তির প্রকাশের সাথে যদি যুক্ত হত তাঁর বয়সের পূর্ণতা ও অভিজ্ঞতা, তাহলে বাংলা সাহিত্য জগৎ বৃহৎ ক্ষেত্রে পূর্ণতা লাভ করতে পারতো। তা সত্ত্বেও সুকান্ত তাঁর অপরিণত যৌবনেই এমন কবিতা লিখে গেছেন যা সুপরিণত এবং এই সকল রচনার মাধ্যমেই তিনি চিরস্মরণীয় হয়ে আছেন।
জনগণের কবি সুকান্তের সমাজ-সচেতনতা, দৃষ্টিভঙ্গি ও সাহসী কলমে তাঁর শক্তির প্রকাশের সাথে যদি যুক্ত হত তাঁর বয়সের পূর্ণতা ও অভিজ্ঞতা, তাহলে বাংলা সাহিত্য জগৎ বৃহৎ ক্ষেত্রে পূর্ণতা লাভ করতে পারতো। তা সত্ত্বেও সুকান্ত তাঁর অপরিণত যৌবনেই এমন কবিতা লিখে গেছেন যা সুপরিণত এবং এই সকল রচনার মাধ্যমেই তিনি চিরস্মরণীয় হয়ে আছেন।

 বিয়াত্রিচকে খুঁজে বেড়ালেন জীবনের ওপারে মরণে, লিখলেন ডিভাইন কমেডি এবং স্বর্গ থেকে বিয়াত্রিচ তাকে blessed life বা পূত জীবনের সন্ধান দিলেন।
বিয়াত্রিচকে খুঁজে বেড়ালেন জীবনের ওপারে মরণে, লিখলেন ডিভাইন কমেডি এবং স্বর্গ থেকে বিয়াত্রিচ তাকে blessed life বা পূত জীবনের সন্ধান দিলেন।










 ষাটের দশকের সাহিত্য আন্দোলন : ষাটের দশকে বাংলাদেশে যে নতুন ধারার সাহিত্য আন্দোলন হয়, তিনি ছিলেন তাঁর নেতৃত্বে। সাহিত্য পত্রিকা কণ্ঠস্বর সম্পাদনার মাধ্যমে সেকালের নবীন সাহিত্য যাত্রাকে তিনি নেতৃত্ব ও দিকনির্দেশনা দিয়ে সংহত ও বেগবান করে রেখেছিলেন এক দশক ধরে। বাংলাদেশে টেলিভিশনের সূচনালগ্ন থেকে মনস্বী, রুচিমান ও বিনোদন-সক্ষম ব্যক্তিত্ব হিসেবে আবির্ভুত হন আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ। টেলিভিশনের বিনোদন এবং শিক্ষামূলক অনুষ্ঠানের উপস্থাপনায় তিনি পথিকৃৎ ও অন্যতম সফল ব্যক্তিত্ব।
ষাটের দশকের সাহিত্য আন্দোলন : ষাটের দশকে বাংলাদেশে যে নতুন ধারার সাহিত্য আন্দোলন হয়, তিনি ছিলেন তাঁর নেতৃত্বে। সাহিত্য পত্রিকা কণ্ঠস্বর সম্পাদনার মাধ্যমে সেকালের নবীন সাহিত্য যাত্রাকে তিনি নেতৃত্ব ও দিকনির্দেশনা দিয়ে সংহত ও বেগবান করে রেখেছিলেন এক দশক ধরে। বাংলাদেশে টেলিভিশনের সূচনালগ্ন থেকে মনস্বী, রুচিমান ও বিনোদন-সক্ষম ব্যক্তিত্ব হিসেবে আবির্ভুত হন আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ। টেলিভিশনের বিনোদন এবং শিক্ষামূলক অনুষ্ঠানের উপস্থাপনায় তিনি পথিকৃৎ ও অন্যতম সফল ব্যক্তিত্ব। বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র : আবদুল্লাহ আবু সায়ীদের ব্যক্তিত্বের প্রায় সবগুলো দিক সমন্বিত হয়েছে তাঁর বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের সংগঠক সত্তায়। তিনি অনুভব করেছেন যে সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ে তোলার লক্ষ্যে আমাদের প্রয়োজন অসংখ্য উচ্চায়ত মানুষ। আলোকিত মানুষ চাই– সারা দেশে এই আন্দোলনের অগ্রযাত্রী হিসেবে প্রায় তিন দশক ধরে তিনি রয়েছেন সংগ্রামশীল। বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র গড়ে উঠেছে একটু একটু করে, অনেক দিনে। এই দীর্ঘ সময়ে বিভিন্ন ঘাত-প্রতিঘাতের মুখে নানা উত্থান পতনের মধ্য দিয়ে তাঁকে এগোতে হয়েছে।
বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র : আবদুল্লাহ আবু সায়ীদের ব্যক্তিত্বের প্রায় সবগুলো দিক সমন্বিত হয়েছে তাঁর বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের সংগঠক সত্তায়। তিনি অনুভব করেছেন যে সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ে তোলার লক্ষ্যে আমাদের প্রয়োজন অসংখ্য উচ্চায়ত মানুষ। আলোকিত মানুষ চাই– সারা দেশে এই আন্দোলনের অগ্রযাত্রী হিসেবে প্রায় তিন দশক ধরে তিনি রয়েছেন সংগ্রামশীল। বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র গড়ে উঠেছে একটু একটু করে, অনেক দিনে। এই দীর্ঘ সময়ে বিভিন্ন ঘাত-প্রতিঘাতের মুখে নানা উত্থান পতনের মধ্য দিয়ে তাঁকে এগোতে হয়েছে। প্রথমদিকে তার তত্ত্বাবধানে মাত্র পঁচিশ জন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রী বিশ্বের মহান সাহিত্য কর্মগুলো পড়তে ও সেগুলোর উপর আলোচনা করা শুরু করে। ধীরে ধীরে এই পাঠচক্রে স্কুল-কলেজ ও সাধারণ মানুষদের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। এই পাঠচক্র গুলোতে বাংলা ও বিশ্ব সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ বইগুলোর পঠন এবং সেগুলোর ওপর প্রাণবন্ত আলোচনা করা হয়। বর্তমানে বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের ৫০০টি শাখা দেশের মোট ৫৪টি জেলায় তাদের কর্মকাণ্ড বিস্তৃত করেছে এবং এর সাথে যুক্ত আছেন বহু স্বেচ্ছাসেবী কর্মী।
প্রথমদিকে তার তত্ত্বাবধানে মাত্র পঁচিশ জন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রী বিশ্বের মহান সাহিত্য কর্মগুলো পড়তে ও সেগুলোর উপর আলোচনা করা শুরু করে। ধীরে ধীরে এই পাঠচক্রে স্কুল-কলেজ ও সাধারণ মানুষদের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। এই পাঠচক্র গুলোতে বাংলা ও বিশ্ব সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ বইগুলোর পঠন এবং সেগুলোর ওপর প্রাণবন্ত আলোচনা করা হয়। বর্তমানে বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের ৫০০টি শাখা দেশের মোট ৫৪টি জেলায় তাদের কর্মকাণ্ড বিস্তৃত করেছে এবং এর সাথে যুক্ত আছেন বহু স্বেচ্ছাসেবী কর্মী।



 উজ্জ্বল আঁধারের উপাখ্যান
উজ্জ্বল আঁধারের উপাখ্যান









 কাজী নজরুল ইসলাম।
কাজী নজরুল ইসলাম।
