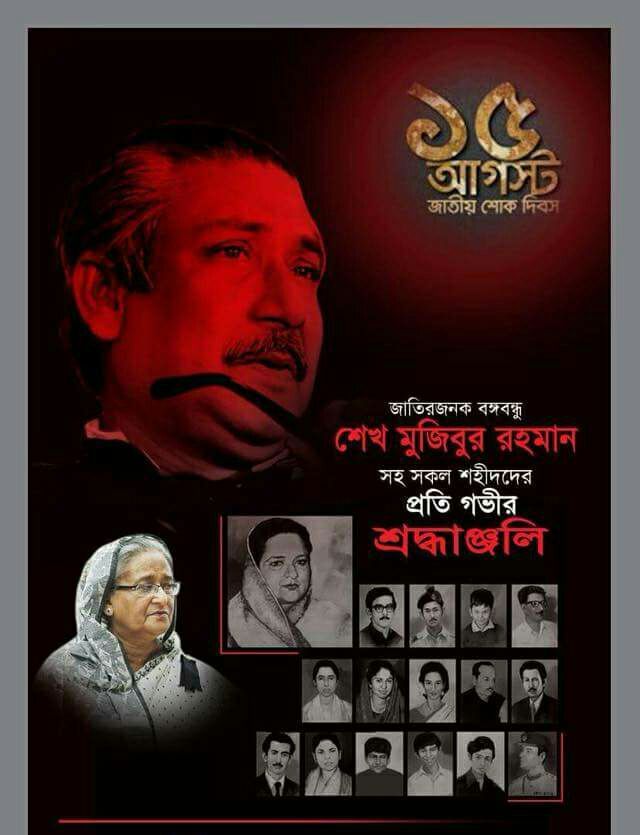আমার বাবা-মা এর রেখে যাওয়া আমি।
আমার পিতার কথা লিখতে গেলে এক পুথি বা রামায়ণ হয়ে যাবে এতে কোন সন্দেহ নেই।
কি নিয়ে লিখব আর কি লিখব না সে কথা ভাবতেই পারছি না। কোথা থেকে শুরু করব তাও বুঝতে পারছি না। যাকে পিতা বলে জেনে এসেছি তাকে যে কোন শ্রেণীর মানুষ হিসেবে ফেলা যায় তাই আমি এখনও বুঝে উঠতে পারিনি। কখনও ভেবেছি তিনি অতি উদার ও মহৎ শ্রেণীর আবার কখনও মনে হয়েছে তিনি অতি রাগি এবং মেজাজি মানুষ। আবার কখনও যে তাকে ধীর স্থির শান্ত প্রকৃতির মনে হয়নি তেমন করেও ভাবার সুযোগ হয়নি। কখনও মনে হয়েছে বাবা খুব অস্থির এবং ছটফটে মেজাজের মানুষ। তবে তিনি যে ধরনের মানুষই হোক না কেন তিনি যে একজন সফল পিতা তাতে কোন সন্দেহ নেই। সফল বলেই হয়ত তার সন্তানেরা আজ পৃথিবীর নানা প্রান্তে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে এবং বেশ সুনাম ও মর্যাদার সাথেই রয়েছে। তার মেঝ ছেলে বিলাতের নেইলসওয়ার্থের ডিসট্রিক্ট কাউন্সিলর এবং অবাক হতে হয় যে সেখানে বাংলাদেশী তো দূরের কথা এশিয়ান বলতে মাত্র তিন ঘর বাসিন্দা। এই ইংরেজ অধ্যুষিত এলাকায় নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি হয়ে বেশ সুনাম ও দক্ষতার সাথে তার মেয়াদ উত্তীর্ণ করেছে।
ছোট বেলায় মার্টিন রোড এলাকায় যখন আমরা থাকতাম তখন আমার বাবাকে ভলি বল খেলতে দেখেছি এবং এখনও মনে পড়ে ওই এক বিকেলে আমার মা কি যেন বানিয়েছিল আর আমি তাই হাতে নিয়ে খেতে খেতে বাসার বাইরে আব্বার খেলা দেখার জন্য কোটের বাইরে দাঁড়িয়েছিলাম আর তাই আব্বার নজরে এলে তিনি খেলা রেখে আমাকে চিলের মত ধরে উঁচু করে বাসায় আমার মার কাছে দিয়ে গিয়েছিলেন। বাইরে কিছু খেতে হয় না একথা আমার মাকে ভাল করে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন এবং পরে এ নিয়ে বেশ অনেকক্ষণ হৈ চৈ করেছিলেন। সেই সাথে আমার মনেও ওই কথাটা এমন ভাবে গেঁথে গিয়েছিল যে আজ আমিও আমার মেয়েদের সেই শিক্ষা দিতে পেরেছি। যদিও সে শিক্ষা এখন আমি রাখতে পারছিনা। বিলাতে থাকার সময় ওদের দেখা দেখি এবং সময়ের মূল্য দিতে গিয়ে হাটতে হাটতে বাগেট বা পিজা বা কেক খেতে খেতে বাস স্ট্যান্ড কিংবা টিউব স্টেশনে গিয়েছি।
আমার পিতাকে কিছু কিছু বাজার করতে দেখেছি সরাসরি আড়ত থেকে। যেমন সবজি, আলু পিয়াজ এই সব বাজার তিনি সপ্তাহ বা কোন ক্ষেত্রে মাসের জন্য এমনকি পুরো বছরের জন্য করে রাখতেন। যে কোন ফলের সিজনে কোন ফল তাকে সের দরে কিনতে দেখিনি, আঙ্গুর, আপেল, আম এবং পেশোয়ায় কাবুল তেহরানে উৎপন্ন নানান জাতের সুস্বাদু ফলমূল তিনি ও দেশের প্রচলিত খেজুর পাতার আস্ত ঝুরি ধরেই কিনতেন এবং বাড়িতে আনার পর আমার মা সেগুলিকে অত্যন্ত যত্নের সাথে নিপুণ হাতে সুন্দর করা সাজিয়ে রাখতেন। আমার মা বাবার সন্তান বলতে গেলে তখন একমাত্র আমিই ছিলাম সবে ধন নীলমণি কাজেই সঙ্গত কারণে আমাকেই ওই সব ফল নামের যন্ত্রণা গিলতে হতো। যদিও আজ ভাবি ইসসস তখন কি আর জানতাম এই সব ফল ফলাদিগুলোকে এক সময় আমাদের দেশে ভিসা নিয়ে যেতে হবে!
আমরা যখন আবিসিনিয়া লাইনে থাকতাম ওই এলাকার কাছেই ছিল করাচী শহরের কসাই খানা। প্রতিদিন দেখতাম শত শত গরু, মহিষ, ভেড়া, দুম্বা আর ছাগল নিয়ে কসাই খানায় যেত আর ওখানে ওগুলি জবাই হয়ে ড্রেসিং হয়ে পৌরসভার সিল লাগিয়ে ভ্যানে করে সমস্ত করাচী শহরে সেগুলি পৌঁছে দিত। সে কি বিশাল কসাই খানা! আমরা বন্ধুরা মিলে মাঝে মাঝেই ঐ কসাই খানা দেখতে যেতাম আর পাঠান দারোয়ান আমাদের ভিতরে যেতে দিতে চাইত না। বলত রক্ত দেখে তোমরা ভয় পাবে। আমরা বলতাম আমরা কি আর তোমার মত ভয়ের ডিপো? আমরা কিছুতেই ভয় পাই না। তাই নাকি? হ্যাঁ, দেখনা আমরা বড় হয়ে গেছি! পাঠান ব্যাটা একটু হেসে আর একজনকে বলে দিত এই ওদের নিয়ে একটু দেখিয়ে আন। সত্যিই কি বীভৎস সে দৃশ্য! বিশেষ কায়দার এতো বড় বড় শিং ওয়ালা গরু মহিষগুলো বিশাল মুছ ওয়ালা দুই জন কসাই ধরে বেল্টের উপর ফেলে বিশাল ছুরি দিয়ে জবাই করে ফেলত। পাশে দেড় ফুট গভীরতার নর্দমা দিয়ে কল কল শব্দ করে রক্তের স্রোত বয়ে যেত। জবাই হয়ে গেলে বেল্ট টেনে নিয়ে যেত চামড়া ছাড়াবার জন্য। একের পরে চলছে এভাবে। ওদিকে চামড়া ছাড়ানো হয়ে গেলে আবার মেশিনে ওগুলো ড্রেসিং হয়ে পাতলা কাপড়ে ঢেকে কভার্ড ভ্যানের হুকে ঝুলিয়ে রাখত। এলাহি কাণ্ড। এখন সেই দৃশ্য মনে ভয়ই করে। আমার বাবা এখান থেকে প্রায়ই একটা রান কিংবা মাথা কিংবা তার পছন্দ মত কোন বড় এক টুকরা নিয়ে গেয়ে নিজেই ছোট ছোট টুকরা করে কেটে কুটে বানিয়ে আমার মার হাতে দিতেন আর মা সেগুলি খুব যত্ন করে কিছু রেখে দিতেন আবার কিছু তখনই রান্না করতেন যেদিন এমন কিছু রান্না হতো সেদিন আমার মা আটা মাখিয়ে একটা থালায় নিয়ে মার হাতে বানান সুন্দর কাপড়ের তৈরি ঢাকনা দিয়ে আমার হাতে দিয়ে বলতেন যা ওই দোকান থেকে রুটি বানিয় নিয়ে আয়। ও দেশে সবাই রুটি খায় বলে রুটি বানাবার দোকান আছে যারা শুধু রু|টি বানিয়ে দেয়। তন্দুরের রুটি। এই দোকানে দেয়ার জন্য আটা মাখাবার ভিন্ন কৌশল আছে। আমার মনে আছে আমার মা বাংলাদেশি বলে ওই কৌশল তার জানা ছিল না তাই দোকানদার আমাকে দেখেই বুঝতে পেরেছিল আর তাই আমার থালা নিয়ে ঢাকনা খুলে বলে দিয়েছিল এটা নিয়ে বাসায় যাও আর তোমার মাকে বল এ ভাবে আটা মেখে দিতে। ঘরে ফিরিয়ে এনে মাকে বললাম। মা তাদের দেখান কৌশলে আবার আটা মেখে দিলে নিয়ে গেলাম। দোকানি তন্দুরের রুটি বানিয়ে দিল। বাসায় এসে সেই কসাই খানা থেকে আনা মাংস রান্না দিয়ে বাবা আমি আর মা কি মজা করে খেয়েছি। আমি নাকি ওদের দেখাদেখি আলু পরটা, মুলা পরটা, মেথি শাক খেতে শিখছিলাম। মার কাছে শুনেছি।
এখনও স্পষ্ট মনে আছে ছোট বেলায় তখন আমরা ফেডারেল এরিয়ায় থাকতাম। দেখেছি বাবা অফিসে যাবার পোশাক পরে বের হতেন আর মা দরজাটা বন্ধ করে তিনতলা বাসার বারান্দায় এসে আমাকে ধরে দাঁড়াতেন। বাবা সিঁড়ি দিয়ে নেমে ডান দিকের রাস্তায় যেখানে বাসের অন্যান্য যাত্রীরা কিউতে দাঁড়াত সেখানে গিয়ে কিউতে দাঁড়াতেন। মা আমাকে দেখিয়ে দিতেন ওই যে দেখ তোমার বাবা। আমি এবং মা বাবার পথের দিকে তাকিয়ে থাকতাম। দেখতাম বাবা এক সময় পিছনে ফিরে দেখে কিউতে দাঁড়াতেন। এই দিন গুলির কথা একটু একটু ঝাপসা ঝাপসা মনে পড়ে। সম্ভবত এর মধ্যে আরও কিছু বড় হয়েছি তখন ওই তিন তলার বাসার এলাকায় থাকতাম না। সে দিনের কথা এখনও স্পষ্ট মনে আছে। আমি তখন বেশ হাটতে পারি। বাবা আমাকে নিয়ে মার্টিন রোড নামে এক আবাসিক এলাকায় এলেন বাসা দেখার জন্য। আগের ওখানে সব দিক দিয়েই ভাল ছিল। খোলা মেলা এলাকা তিন তলা সব দালান। বেশ ফাঁকা এলাকা কিন্তু বাবার অফিস অনেক দূর হয়ে যায় বলে এই মার্টিন রোড এলাকায় বাসা দেখতে এসেছেন।
ছোট বেলার একটা কথা আমার সবসময় মনে পড়ে। বাবার কথা বলতে হলে এই কথাটি সবসময় মনে হয়। করাচী শহর সমুদ্রের পাড়ে হলেও এখানে ভীষণ শীত। একদিন এমনি এক শীতের সন্ধ্যায় আমার বয়সী এক বিকলাঙ্গ ছেলে শীতে কাঁপতে কাঁপতে ভিক্ষা করছে। ছেলেটি আমাদের বাসায় নক করলে বাবাই দরজা খুলে দেয় এবং ছেলেটিকে এভাবে কাঁপতে দেখে ওকে বাসার ভিতর নিয়ে এসে চুলায় আগুন জ্বেলে ওকে আগে গরম করে নিয়ে আমার মাকে বলে দুধ গরম করিয়ে ওকে খাইয়ে তারপরে আমার মায়ের বানানো নতুন কফি কালারের ফুল হাতা সোয়েটারটা আমার গায়ে থেকে খুলে ওকে দিয়েছিল। লক্ষ করে দেখেছি আমার মেয়েগুলি হয়েছে এমন। ওরা প্রচণ্ড গরমে বা শীতে যে রিকশায় করে বাইরে থেকে বাড়িতে ফিরে সেই রিকশা চালককে আগে বাড়ীতে পৌঁছে কিছু খাইয়ে নেয় হাতের কাছে থাকলে কাপড় চোপর কিছু দিয়েও দেয় আবার ভাড়া দেয়ার সময় কিছু বেশিই দিয়ে দেয়। দেখি আর ভাবি জেনেটিক ধারা বোধ হয় একেই বলে।
বড় হবার পর যেদিন আমাকে আমার প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে রেখে আসেন সেদিন বাবার এই আশ্চর্য চেহারা দেখে অবাক হয়ে গিয়েছিলাম। বাবা চাননি আমি এই সময়ে কাজ শুরু করি কিন্তু তখনকার দেশের বর্তমান প্রেক্ষাপটে পরিস্থিতির কারণে নিরুপায় বাবা এই ব্যবস্থা বাধ্য হয়ে মেনে নিয়েছিলেন এবং তাতে কতটা ব্যথা পেয়েছিলেন সে দেখলাম যখন তিনি আমাকে রেখে ফিরে আসছিলেন। যে বাবাকে কোনদিন কাঁদতে দেখিনি সেই বাবার চোখ দিয়ে টল টল করে পানি ঝরছিল এবং সে চোখের পানি আমার চোখে ধরা পরার ভয়ে তিনি ঘুরে দাড়িয়ে কিছু না বলে সামনের দিকে হাটা সুরু করেছিলেন। ছোট বেলায় জ্বর হলে দেখেছি সারা রাত জেগে পাশে বসে থেকে আবার সকালে যথারীতি অফিসে চলে যেতেন। একটু বিশ্রাম নিতে দেখিনি। তখন ভাবতাম আমাকে এভাবে রেখে বাবা কেন অফিসে যায়? ছোট বেলায় আমি প্রায়ই নানান অসুখে ভুগতাম আর হেটে যেতে পারব না বলে বাবা আমাকে কোলে নিয়েই ডাক্তারের কাছে নিয়ে যেতেন।
ঈদের সময় মনে আছে অফিস থেকে ফিরে রোজা রেখে আমাদের জামা ক্লথ মার্কেটে নিয়ে যেতেন। নিজের পছন্দ মত পোশাকের কাপর, খেলনা নানা কিছু কিনে দিতেন। জিজ্ঞেস করতেন দেখ তোমার কোনটা পছন্দ হয়। মা আবার সেই কাপড় কেটে নিজেই জামা প্যান্ট সেলাই করে দিতেন। ঈদের দিন আবার নিজের ইচ্ছে মত খরচ করার জন্য নামাজ পড়ে এসে কিছু টাকাও দিতেন। দেয়ার আগে জিজ্ঞেস করতেন কত দিতে হবে। তখন যদিও টাকার হিসাব বুঝতাম না বলে কিছু বলতাম না। আমার একটা নেশা ছিল কলম হারাবার। এখনকার মত তখন পাঁচ টাকায় কলম পাওয়া যেত না বা সস্তা কলমও বাবা কিনতেন না কিন্তু আমি আমার নিয়ম অনুযায়ী একদিনের বেশি সে কলম রাখতে পারতাম না হারিয়ে ফেলতাম। একবার আমার জন্য, মায়ের জন্য এবং তার নিজের জন্য একসাথে তিনটা খুব সুন্দর কলম এনেছিলেন এবং বন্ধুদের দেখাবার জন্য বিকেলে খেলতে যাবার সময় ওই তিনটা কলমই এক সাথে পকেটে নিয়ে গিয়েছিলেম এবং ফলাফল গতানুগতিক। হারিয়ে ফেলেছিলাম। বাসায় ফিরে আসার পর বাবা কিছুই বললেন না দেখে অবাক হলাম বাবা কিছুই বল না? একটু নয় বেশ অবাক হয়ে কিছুতেই বিশ্বাস করতেই পারছিলাম না। কয়েক দিন পরে মাকে সে কথা জিজ্ঞেস করলাম আচ্ছা আম্মা আমি যে সেদিন কলম হারিয়ে ফেললাম আব্বা যে কিছু বলল না! মা বললেন তুমি যে হারাওনি তাতেই তোমার বাবা খুশি তাই কিছু বলেনি। তেমনি করে আমার মেয়েরাও যখন ছোট বেলায় কিছু হারিয়ে ফেলত বা ভেঙ্গে ফেলত তখন ওরা অনুতপ্ত হয়ে কেঁদে ফেলত আর আমি ওদের কোলে নিয়ে বা বুকে টেনে নিয়ে বলতাম কি হয়েছে মা এতে কাঁদতে নেই তুমি যে ভাল আছ এই আমার জন্য যথেষ্ট। বড় মেয়ে এসএসসি পরীক্ষায় বিজ্ঞান পরীক্ষা খারাপ দিয়েছিল আর সেদিন আমি ওর এই পরীক্ষা খারাপ হবার জন্য আইসক্রিম কিনে দিয়েছিলাম যাতে সে মন খারাপ করে পরের পরীক্ষা খারাপ না করে। সেই বাবাকে বড় হয়ে বিদেশ থেকে অন্যান্য জিনিসের সাথে একটা ছাতা এনে দিয়েছিলাম আর তিনি সে ছাতা হারিয়ে এসে খুব বিষণ্ণ মনে মাকে জানিয়েছিল সে ঘটনা। আমি যে ছেলের ছাতা হারিয়ে আসলাম! ও যখন জানতে চাইবে তখন কি বলব? শুনে আমার ছোট বেলার সেই সব দিনের কথা মনে হলো যখন আমি এক সাথে তিন কলম হারালেও বাবা কিছু বলেনি। আমি বলেছিলাম কি হয়েছে তাতে একটা ছাতা হারিয়েছেন আমি দশটা ছাতা কিনে দেব। আপনার চেষ্টায় আপনাদের দোয়ার বলেই আমি এই যোগ্যতা অর্জন করেছি আর আমার বাবার চেয়ে কি একটা ছাতার দাম বেশী হয়ে গেল? কথাটা সুনে আমার মা আমাকে বুকে টেনে নিয়ে আদর করে বলেছিলেন এইতো একেবারে বাবার মত কথা বলতে শিখেছে আমার বাবা! বাবা মায়ের এই দোয়া কি বিফলে যেতে পারে?
হজে যাবার আগে ভিসার আবেদন করার সময়ে নেয়া ছবি। মায়ের মৃত্যুর পরে বাবা মায়ের দুটি ভিন্ন ছবিকে একত্রে এনলার্জ করে বাঁধান ছবি থেকে নেয়া ছবি। এমন দেয়ার মত ছবি নেই যা আছে সে স্ক্যান করা ছাড়া দেয়া যাবে না।
আমি তখন দেশে চাকরি করি। একবার বাসার স্প্রিং ও রেক্সিনের সোফা মেরামত করালাম বেশ দামি রেক্সিন দিয়ে। সরকারি চাকরি জীবীদের হিসেবে বেশ অনেক টাকা খরচ হয়েছিল। যেদিন মেরামত শেষ হলো সেদিন মিস্ত্রিরা কাজ শেষ করে বলল দেখেন স্যার আমাদের কাজ শেষ এখন আমাদের বিদায় দেন। ওদের প্রাপ্য টাকা গুনে দিলাম ওরা সিরি দিয়ে নেমে চলে গেল। ভাবলাম দেখি কেমন হলো। ভিতরে এসে দেখি একটা সিঙ্গেল সোফার সিটের মাঝ খানে অনেক খানি কাটা। দেখেই আমার প্রাণ শুদ্ধ চমকে উঠল। কি ব্যাপার নতুন মেরামত করা সোফা এমন হলো কি করে? ভাবছি এমন সময় রুমের বাইরের বারান্দায় শুনলাম খচ খচ শব্দ হচ্ছে। দরজা দিয়ে দেখলাম ছোট মেয়ে কি করছে। আব্বু বলতো সোফাটা এমন হলো কি করে? আব্বু তুমি জান না ওটা আমি করেছি!
কেন?
দেখলাম কাটে নাকি!
আমি অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলাম।
মেয়ে বলে কি? কেন কাটলে?
দেখলাম কাটে না কি!
কি দিয়ে কেটেছ?
ব্লেড দিয়ে!
অবাক হয়ে মেয়ের দিকে তাকিয়েই রইলাম। কিছুই বললাম না। ভাবলাম ও সত্যি কথা বলেছে এবং সত্যি বলার সাহস ওর আছে। কাজেই একে কিছুই বলা সঙ্গত হবে না। শুধু জিজ্ঞেস করলাম কাজটা কি ভাল করেছ?
না আব্বু, আমি ভাবতে পারিনি যে ওটা কেটে যাবে!
এই মেয়েকে কি কিছু বলা যায়? রেক্সিনের টুকরো দিয়ে আঠা লাগিয়ে ওটা মেরামত করে নিলাম। আমার বাবাও আমাদের এমন কোন কাণ্ড ঘটলেও কিছু বলতেন না। তাই আমিও ওকে কিছু বলতে পারলাম না।
আবিসিনিয়া লাইনের বাসর ভিতরে বাগানে একটা বিশাল সজনে গাছ ছিল বারান্দায় খেতে বসলে ওই গাছের ছায়া পরত। গাছের ডালে নানা জাতের পাখি এসে বসত দেখতে খুব ভাল লাগত। খেতে বসলে আমি অনেক হাঙ্গামা করতাম কিছুতেই খেতে চাইতাম না। খাবার প্রতি আমার খুবই অনীহা ছিল। আমি এসএসসি পরীক্ষা পর্যন্ত মায়ের রান্না ছাড়া কারও রান্না খেতে চাইতাম না। যাই হোক যা বলছিলাম মা প্লেটে যা দিতেন তার থেকে একটু খেয়েই রেখে উঠে যেতাম, আর ভাল লাগছে না মা আর খাব না। বাবা তখন প্লেটটা নিজের কাছে নিয়ে বলতেই দেখি কি ভাল লাগে না! আমার কাছে আস, দেখত ঐ ডালে কি সুন্দর পাখি বসেছে! যেই পাখির দিকে তাকাতাম আর অমনি বাবা তার প্লেট থেকে কিছু মাখান ভাত আমার প্লেটে দিয়ে বলতেন ঠিক আছে খেতে না চাইলে খেয়ো না কিন্তু এই যতটা ভাত মাখিয়েছ সেটুক খেয়ে ফেল। আচ্ছা খাচ্ছি। এই করতে করতে দেখতাম আমার প্লেটের ভাত শেষ হচ্ছে না। তখন মা বাবা দুইজনের হাসি দেখে অনুমান করতাম কোন চালাকি হয়েছে কিন্তু কি হয়েছে তখন বুঝতাম না। পরে একদিন আব্বা যেদিন ধরা পরে গেলেন সেদিন বুঝলাম।
ঈদের দিন সকালে মা গোসলের পানি গরম করে দিলে বাবা আমার সব ভাই বোনদের একে একে গোসল করিয়ে দিতেন। সে প্রক্রিয়া রীতি আমার মেয়েদের বেলায় আমিও করেছি। তখন বাবার কথা মনে হতো। আবার এমন অনেক কাজ যা তিনি আমার জন্য করেছেন আমিও আমার সন্তানদের জন্য তেমন করেই করার চেষ্টা করেছি। এইতো সেদিন ৬ই জুন তারিখে বাবাকে এগিয়ে আনার জন্য এয়ারপোর্ট গেলাম। এয়ারপোর্টে ১ নম্বর টার্মিনালে দাঁড়িয়ে ভাবছিলাম এই এয়ারপোর্টে আমার বাবা এক সময় আমাকে রিসিভ করার জন্য আসতেন আর তাকে নেয়ার জন্য আজ আমি এসেছি আমার স্ত্রী সন্তানকে নিয়ে। আমার বাবা ইংল্যান্ড আর কানাডায় তার সফল ছেলেদের কাছে থেকে আসলেন প্রায় এক বছর। আমার স্ত্রী জিজ্ঞেস করল কি ভাবছ? তখন তাকে বললাম সেই যেবার গ্রিস হয়ে এসেছিলাম তখন বিমানের ফ্লাইট দুই দিন দেরি করে এসেছিল এবং আমি কোন ভাবেই বাসায় জানাতে পারছিলাম না ফ্লাইট কখন পৌঁছাবে। কাজেই আমার বাবা বিমানের প্রতিটা ফ্লাইটে এসে এয়ারপোর্ট থেকে বিমানের প্যাসেঞ্জার লিস্ট দেখে ফিরে ফিরে গেছে। আর আজকে আমার বাবার একটু দেরি হচ্ছিল বলে আমার কেমন বিরক্ত লাগছে। যদিও মেয়েকে ভিতরে পাঠিয়ে আমরা বাইরে অপেক্ষা করছিলাম। একটু পরে পরেই মেয়ে মোবাইলে খবর দিচ্ছিল না আব্বু দাদাকে দেখছিনা ওদিকে ভিড় কমে আসছে। শেষ পর্যন্ত একসময় দেখলাম হুইল চেয়ারে করে আমার মেয়ে তার দাদাকে নিয়ে বেরিয়ে আসছে।
আমার বইটি যখন প্রকাশ হয় তখন তিনি কানাডার টরন্টোতে ছিলেন। ওখানে আমার ছোট ভাইয়ের বৌ সোহানা তার শ্বশুরকে জিজ্ঞেস করেছিল “আব্বা দাদার বই বের হয়েছে আজ, এ কথা জেনে আপনার কেমন লাগছে?” ” কেমন লাগবে ছেলের বই প্রকাশ হলে কোন বাবার ভাল না লাগে বল!” ওখানে থাকতে আমার ব্লগে লেখা কিছু কিছু গল্প সোহানা এবং লন্ডনের সেঝ ভাইয়ের বৌ সোমা পড়ে শোনাত এবং সেগুলি খুব মনোযোগ দিয়ে শুনতেন। দেশে ফিরে আসার পর বইটা বাবার হাতে দিয়ে একটা আশ্চর্যের বিষয় লক্ষ করলেম যে যে বাবাকে কেবল মাত্র ধর্মীয় বই ব্যতীত ভিন্ন কোন বই পড়তে দেখিনি সেই তিনি তার ছেলের বইটি দুই দিনের মধ্যেই শেষ করে ফেললেন! তার পাঠ প্রতিক্রিয়া বুঝলাম ‘ আর কিছু লিখেছিস? হ্যাঁ আব্বা লিখেছি এবং লিখছি, এখন এটাই আমার একমাত্র নেশা। সামনে কি আর কোন বই প্রকাশ হবে? সবাই বই প্রকাশ করলে সাধারনত দেখা যায় সাহিত্য অঙ্গনে কোন নামি ব্যাক্তিত্ব বা কোন মহাজন কিংবা কোন মন্ত্রি-নেতাদের দিয়ে বইয়ের মোড়ক উন্মোচন অনুষ্ঠান করে কিন্তু আমি করেছি আমার বাবা আর স্ত্রীকে দিয়ে (তখন আমার মা জীবিত ছিলেননা)। স্ত্রীকে করিয়েছি এইওজন্য যে, সে আমাকে লেখার ব্যাপারে সকল রকমের সহযোগিতা না করলে আমি কোনদিনই কিছু লিখতে পারতামনা। লেখার সময় সে কোনদিনই কোন কাজের কথা বলেনি দরকার হলে সে নিজে বাজারে গিয়ে বাজার করে এনেছে কিন্তু আমাকে বিরক্ত করেনি।
এই বাবাকে নিয়ে লিখলে অনেক লিখা যায় কিন্তু বাবার কথা কি আর এমন পরিসরে লিখা যায়? বাবার ভাল মন্দ কত কি আছে কত কি নিয়ে একজন মানুষ বাবা হয়। একজন মানুষ মন্দ হলেই যে সে মন্দ বাবা হবে এমন কেউ বলতে পারে কি? এক জন মন্দ স্বামী হতে পারে, মন্দ মানুষ হতে পারে কিন্তু কক্ষনো মন্দ বাবা হতে পারবে না! আজ নিজে বাবা হয়ে বুঝতে পারছি একজন বাবা তার সন্তানের জন্য কতখানি ত্যাগ আর পরিশ্রম করেন। আমি যেদিন বাবা হলাম সেদিন আমি দেশ থেকে অনেক দূরে। প্রায় একমাস পরে বাবা হবার খবরটা জানতে পেরে মনে হচ্ছিল তক্ষুনি ছুটে আসি, মনে হচ্ছিল আমার কেন এক জোড়া পাখনা নেই, কেন আমি আজ উড়ে যেতে পারছি না? কেন আমার এত ত্যাগের বিনিময়ে পাওয়া আমার প্রথম সন্তানকে দেখতে পারছি না? যেদিন দেশে ফিরে এসেছি পরে আমার সন্তানের মা পাশে বসে তাকে আমার কোলে তুলে দিল তখন মেয়ে একবার ওর মায়ের দিকে আবার আমার দিকে দেখছিল তখনই বুঝলাম এই ছয় মাসের শিশু বুঝতে পেরেছে সে তার কোন ঘনিষ্ঠ একজনের কোলে এসেছে। একটুও কাঁদেনই, বা আমার কাছে থাকতে একটুও আপত্তি করেনি। মায়ের কোলে যেমন ছিল তেমনি বাবার কোলে শুয়ে রইল বাবার মুখের দিকে তাকিয়ে। আমরা কেবল মায়ের কথাই ভাবি কিন্তু বাবার অবদান যে কতখানি সে কেবল একজন বাবাই বুঝে। আমার মনে হয় মা কিংবা বাবা কেউ কিছুতে কম না। সারা দিন আপ্রাণ চেষ্টা করেও যে মহিলা তার স্বামী, শ্বশুর শাশুড়ি বা এই বাড়ির আর কারো মন জোগাতে পারেনি শুধু পেয়েছে অবহেলা, অবজ্ঞা আর নির্যাতন সেই মহিলা তার সন্তানের কাছে মহারানীর সম্মান পেয়ে ধন্য হয়েছে, আনন্দে আপ্লুত হয়েছে।
তবুও বলব সন্তানের জন্য বাবার চেয়ে মায়ের প্রয়োজনটাই বেশি। আমিও একদিন আমার স্ত্রীকে লন্ডনের হিথরো এয়ারপোর্টে দাঁড়িয়ে বলেছিলাম তুমি দেশে ফিরে যাও। আমাদের মেয়েদের জন্য আমার চেয়ে তোমার প্রয়োজনটাই বেশি। আবার একথাও ভাবি যে একজন সন্তান ঈদের আগে বাবার গলা জড়িয়ে ধরে ঈদের পোশাকের চাহিদা জানাবার মধ্যে যে তৃপ্তি পায় সে তৃপ্তি আর কারো কাছে পায় না। বাবাও তার ছেলে মেয়েদের চাহিদা মিটিয়ে সন্তানের মুখে হাসি দেখে যে তৃপ্তি পায় সে তৃপ্তি পৃথিবীর আর কিছুতে পায় না। যে সংসারে মা বাবার মধ্যে সু সম্পর্ক আছে সে সংসারের সন্তানেরা একটা স্বর্গীয় সুখ নিয়ে বেড়ে উঠে। আরও একটা কথা জেনেছি, পৃথিবীর সবচেয়ে নিঃস্ব পিতাও তার সন্তানকে যেমন ভালবাসে পৃথিবীর সবচেয়ে ক্ষমতাধর এবং ধনী পিতাও তার সন্তানকে ততটাই ভাল বাসে শুধু প্রকাশ ভঙ্গির তারতম্য হয়, এ ছাড়া বাকী সবই এক।







 তিনি হলেন ঈশ্বর চন্দ্র বিদ্যাসাগর। ঈশ্বর চন্দ্র বিদ্যাসাগর উনিশ শতকে অবিভক্ত বাংলায় শিক্ষা ও সমাজ সংস্কারে আত্মনিয়োগ করেছিলেন। তিনি হিন্দু সমাজে বিধবা বিবাহ প্রথা চালু করেন। তার প্রচেষ্টায় ২৬ জুলাই ১৮৫৬ সালে বিধবা বিবাহ আইন পাস হয়। নিজের ছেলের সঙ্গে এক বিধবা কন্যার বিয়ে দিয়েছিলেন। যাতে অন্যান্য হিন্দুরাও উৎসাহ বোধ করে। বিদ্যাসাগরের এ আইনের ফলে বঙ্গ-ভারতের কোটি কোটি বিধবাদের স্বামীর ঘরে আশ্রয় হয়েছিল। ঈশ্বর চন্দ্র বিদ্যাসাগর কলকাতা মেট্রোপলিটন কলেজের প্রতিষ্ঠাতা। এ কলেজের বর্তমান নাম ‘বিদ্যাসাগর কলেজ’, কর্মজীবনে ঈশ্বর চন্দ্র ছিলেন কলেজশিক্ষক। তিনি ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের পণ্ডিত ছিলেন। এরপর তিনি সংস্কৃতি কলেজের সহকারী সম্পাদক ও সংস্কৃতের অধ্যাপক হন। কিছু দিন পর তিনি সংস্কৃত কলেজের প্রিন্সিপালের দায়িত্ব পালন করেন।
তিনি হলেন ঈশ্বর চন্দ্র বিদ্যাসাগর। ঈশ্বর চন্দ্র বিদ্যাসাগর উনিশ শতকে অবিভক্ত বাংলায় শিক্ষা ও সমাজ সংস্কারে আত্মনিয়োগ করেছিলেন। তিনি হিন্দু সমাজে বিধবা বিবাহ প্রথা চালু করেন। তার প্রচেষ্টায় ২৬ জুলাই ১৮৫৬ সালে বিধবা বিবাহ আইন পাস হয়। নিজের ছেলের সঙ্গে এক বিধবা কন্যার বিয়ে দিয়েছিলেন। যাতে অন্যান্য হিন্দুরাও উৎসাহ বোধ করে। বিদ্যাসাগরের এ আইনের ফলে বঙ্গ-ভারতের কোটি কোটি বিধবাদের স্বামীর ঘরে আশ্রয় হয়েছিল। ঈশ্বর চন্দ্র বিদ্যাসাগর কলকাতা মেট্রোপলিটন কলেজের প্রতিষ্ঠাতা। এ কলেজের বর্তমান নাম ‘বিদ্যাসাগর কলেজ’, কর্মজীবনে ঈশ্বর চন্দ্র ছিলেন কলেজশিক্ষক। তিনি ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের পণ্ডিত ছিলেন। এরপর তিনি সংস্কৃতি কলেজের সহকারী সম্পাদক ও সংস্কৃতের অধ্যাপক হন। কিছু দিন পর তিনি সংস্কৃত কলেজের প্রিন্সিপালের দায়িত্ব পালন করেন।